৩০ পৌষ ১৪৩২
ভূমিকম্প : বাংলাদেশে ভয়াবহ বিপদ তো সামনে
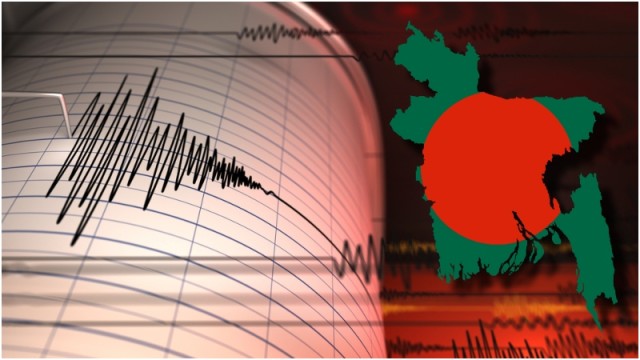
২১ নভেম্বর, সকাল। আকাশে ধূসর কুয়াশা, পরিবেশে ধোঁয়াচ্ছন্নতা।
হঠাৎ ছোট কম্পন অনুভূত হলো, যা ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, টঙ্গী ও নরসিংদী পর্যন্ত আতঙ্ক ছড়াল। কেউ বললেন, “মনে হলো বিল্ডিং দুলছে।” অন্যরা আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, বড় ধসও নামতে পারে।
এই ক্ষুদ্র কম্পনও স্মরণ করালো—প্রকৃতি কখনো সতর্ক না করেই পরীক্ষা নিতে পারে, আর আমরা বারবারই দুর্বল প্রমাণিত হয়েছি। ৫.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্প একটি সরাসরি সতর্কবার্তা। ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এটি দ্রুত আতঙ্ক এবং প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। তবে উদ্ধার প্রক্রিয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটি এক লাইভ ‘স্ট্রেস টেস্ট’, যা বড় ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে।
পুরান ঢাকার ঝুঁকি:
পুরান ঢাকা বহু পুরোনো ইট ও সুরকির নির্মাণে তৈরি এবং প্রায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ির ফ্লোর বৃদ্ধি হয়েছে। Unreinforced Brick Masonry (URM) ভবনগুলোর ভূমিকম্প-সহনশীলতা খুব কম। সংকীর্ণ রাস্তা ও গলিপথ উদ্ধার কাজকে আরও জটিল করবে।
বিল্ডিং কোড ও নির্মাণ মান:
বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) ভূমিকম্প-সহনশীল ডিজাইন নির্দেশ করে। কিন্তু অনেক ভবন কোড মেনে তৈরি হচ্ছে না। আবাসিক এলাকার গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তা যথাযথ নয়। ধ্বংসের সময় বড় অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা রয়েছে।
ভূ-ভৌগোলিক ঝুঁকি:
ডাউকি, মধুপুর ও প্লেট-বাউন্ডারি ফল্ট সক্রিয়। ডাউকি ফল্ট প্রায় ৩০০ কিমি লম্বা এবং বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। ঢাকা শহরের নরম ও ভেজা মাটি কম্পনকে বাড়িয়ে দিতে পারে (যেমন লিকুইফ্যাকশন)।
বড়-মাত্রার ভূমিকম্প সম্ভাবনা:
দ্রুত নগরায়ন, ভুল মাটি ব্যবহার, বিল্ডিং কোড উপেক্ষা combined হলে বড় কম্পনের প্রভাব মারাত্মক হবে। ডাউকি ফল্টে প্রতি বছর প্রায় ১.৬ সেমি শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বড় ভূমিকম্পে রূপ নিতে পারে।
জনসচেতনতা ও আতঙ্ক:
ভূমিকম্প সম্পর্কে মৌলিক সচেতনতা অনেকের নেই। জরুরি অ্যাকশন পয়েন্ট (যেমন ‘ডাক-কভার-হোল্ড’) জানে এমন মানুষের সংখ্যা সীমিত। মিডিয়া এখনো নিয়মিত জনসচেতনতা প্রচার করছে না।
সরকারি প্রস্তুতি:
অনেক ভবন BNBC অনুসরণ করছে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রশিক্ষণ চলছে, কিন্তু দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তি পর্যাপ্ত নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, building code enforcement এবং ঝুঁকিপ্রবণ ভবনগুলোর নজরদারি জন্য শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রয়োজন।
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা:
বড় ভূমিকম্পে হাসপাতাল ও জরুরি সেবা কেন্দ্র চাপের মুখে পড়বে। চিকিৎসা, অ্যাম্বুলেন্স ও উদ্ধার টিমের সংকট রয়েছে। রক্ষাকবচ ও স্থানান্তর ব্যবস্থায় ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।
নগর পরিকল্পনা ও নিরাপদ আশ্রয়:
ঢাকায় খোলা জায়গা সীমিত। ভূমিকম্পের সময় জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রের জন্য পার্ক, খোলা মাঠ বা মুক্ত এলাকা প্রয়োজন। নগরায়নে ভূমিকম্প-সহনশীল ডিজাইন বাধ্যতামূলক করতে হবে, শুধু ভবনের উচ্চতা নয়, ভিত্তি, মাটি গঠন ও ঘনত্ব মাথায় রেখে।
সতর্কবার্তা:
ভবিষ্যতে বড় ভূমিকম্প হতে পারে। নগরায়ন, অবকাঠামো ঘাটতি, জনসংখ্যা ঘনত্ব ও প্রশাসনিক দুর্বলতা এই প্রভাব বাড়াবে। এখনই সময় যথাযথ প্রস্তুতি গড়ে তোলার।
এসআর




মন্তব্য করুন: